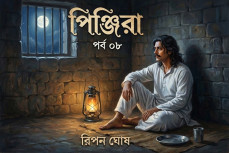
প্রয়োজনের নজরুল
কবির জন্মদিনে আমার প্রণতি
প্রকাশিত: ২০২৫-০৫-২৬ ১৫:০২:৩৫

নিরঞ্জন দে:
আমাদের গালাগালিটা আর গলাগলিতে পরিণত হলো না। একই বৃন্তের কুসুম আদৌ কি হতে পারলাম আমরা! কুসুম তো এখন দুটো নয় অসংখ্য! অসংখ্য কুসুম তো একই বৃন্তে ধরে না।
কবি চেয়েছিলেন আমাদের হ্যান্ডশেক করাতে। কালের আবর্তে আমরা বরং হাতের কনুইয়ের সদ্ব্যবহার করতে পারঙ্গম হয়েছি। আমরা মনোজগতেই খণ্ডিত ও বিভাজিত হাজার বছর ধরে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাতপাত, নারী পুরুষ, আশরাফ আতরাফ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বাঙালি পাহাড়ি কতো বিভাজন আমাদের! মাঝে মাঝে কিছু মহামানব এসে সত্য উপলব্ধি করে আমাদের চিন্তা-চেতনায় অখণ্ড ভাবনা ঢুকানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সফল হননি। কবি নজরুল সেই অখণ্ড ভাবনার অগ্রপথিক ছিলেন। বিভেদ নয় মিলনের কথা বলেছেন, গালাগালি নয় গলাগলির কথা বলেছেন। মানুষ পরিচয়ে, বাঙালি পরিচয়ে আমাদের অখণ্ড রাখার অকৃত্রিম চেষ্টা করে গেছেন তিনি। আমরা কি সেটা ধারণ করতে পেরেছি? কতজন পারছি?
আমি মানুষ, আমি বাঙালি, বাংলাদেশি যা-ই বলি, যে পরিচয়েই ডাকি নিজেকে, আমি চাই গোটা দেশের মানুষকে নিয়ে অখণ্ড চিন্তা-চেতনায় বুক টান করে দাঁড়াতে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠে না। মুখে মুখে কবিতা বলে, গান গেয়ে আর নজরুলকে নিয়ে একটা ঝড়ো সংলাপ ছেড়েও তা হয় না। এক প্রবল উন্মত্ত ঢেউ আমার সমস্ত শুভচিন্তা, সমস্ত আবেগ, সমস্ত অখণ্ড ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মতো। আমাকে ঠেলে দেয় আমার ক্ষুদ্র পরিচয়ের দিকে, মনে করিয়ে দেয় বার বার বিচিত্র বিভীষিকায়।
নজরুলকে আমি জীবিকায় নিতে পারি, গবেষণা করে একাধিক বই লিখতে পারি, মালা ও উত্তরীয় গলায় নিয়ে - কবি নজরুল এটা বলেছেন, ওটা করেছেন, সেটা লিখেছেন বলে বিশাল তথ্য সমৃদ্ধ একটা বক্তৃতাও দিতে পারি; কিন্তু আমি নিজে কিছুই করি না। নজরুলকে জীবনে জড়াতে পারি কতোটা? কতোটা তাঁকে ধারণ করি? এ আত্ম-জিজ্ঞাসাটুকুও আমাদের নেই? আর যাইহোক এমন বিভাজিত সত্তা নিয়ে অখণ্ড নজরুলকে ধারণ করা চরম মূর্খতা। এ মূর্খতায় আমার আনন্দ, আড়ম্বর, আস্ফাল, আত্মতৃপ্তি, আত্মপ্রচার, আত্মপ্রতিষ্ঠা যা-ই থাকুক দিন শেষে আমি চশমা পরা অন্ধ।
যখন কোনো সমাজে উপকরণের গর্বই প্রধান হয়ে সজোরে গলা ফাটায় তখন আত্মার খোঁজ কেউ রাখে না। সেই অলীক গর্বে আত্মা খর্ব হয়, মলিন হয়, নিভৃতে চাপা পড়ে। কবি নজরুল আমার সেই আত্মার ধন। বিভাজিত, খণ্ডিত হওয়ার গ্লানি নিয়েও আমি তাঁকে আগলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি জীবনের অর্ধেক সময় খরচ করেও। তাকে আমার প্রয়োজন।
কবি নজরুলও আমাদের প্রয়োজনে আছেন সর্বত্র। প্রেম নিবেদনে, পাণ্ডিত্যে, আচারে, বিচারে, রাজনৈতিক ভাষণে, নিজেদের আদর্শ প্রচারে, ধর্মের সুবিধাজনক ব্যাখ্যায়, ব্যবসাবাণিজ্যে, সম্প্রদায়গত চিন্তায়, উৎসবে, পূজাপার্বণে কোথায় নেই তিনি! যেটুকু দরকার সেটুকু নিলেই হলো ঠিকঠাক। তাঁর কাছ থেকে নেয়ার মতো জিনিসের তো অভাব নেই। তাঁর উদার হৃদয়টা মাপা আমাদের সাধ্যে কোলায়নি কখনো, আর কবে হবে জানি না। একজন খাঁটি মানুষ, খাঁটি বাঙালি, খাঁটি শিল্পী ও কবি ছিলেন তিনি। নিজেকে তিনি অতি সাধারণ থেকে তুলে এনে কোথায়, কোন উচ্চতায় স্থাপন করে গেছেন সেটা অনুধাবন করার বিষয়। খাঁটি প্রেম ছাড়া সেটা বুঝা অসম্ভব। আত্মশুদ্ধি ছাড়া সেটা অনুধ্যান করা অসম্ভব।
মনের গহীনের নজরুল আর সেমিনারের নজরুল এক নন। হাততালি পাওয়া গান, কবিতার নজরুল আর অন্তরে আসন পেতে বসা নজরুল এক নন। একটা পুঁথিপুস্তক থেকে, শিক্ষকের কাছ থেকে, দেখে শুনে পাওয়া আর মুখস্থ বিদ্যা। ওপরটি সমস্ত মাধ্যম থেকে নিরন্তর অর্জনের ফলে নিজের মতো করে পাওয়া, অখণ্ড পাওয়া, স্নিগ্ধতায় পাওয়া, প্রেমের অথৈ জলে ডুব দিয়ে পাওয়া। যেখানে তিনি নীরবে কানের কাছে এসে বলেন, “আমি বাতাস হইয়া জড়াইবো কেশ, বেণী যবে যাবে খুলিতে...” এমন নিখাদ প্রেম নজরুল ছাড়া আর কে শিখিয়েছেন বাঙালিকে সহজ করে! আবার যিনি সময়ের দাবিতে বিদ্রোহী ভৃগু হতেও ভুলেননি! অগাধ প্রেমের আত্মবিশ্বাস না থাকলে কি ভগবান বুকে পদচিহ্ন আঁকার স্পর্ধা কারো হয়! প্রতিবাদের শক্তিটাও অতল প্রেমের উৎস থেকেই আসা। ভুখা-নাঙা পরাধীন মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল, ভালোবাসা ছিল বলেই সেটি অপ্রতিরোধ্য দ্রোহে পরিণত হয়ে রাজশক্তিকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে। আজ প্রেমহীন হয়ে নীরস শব্দ চয়নে যেটুকু হয় তা শুধুই আবরণ, শুধুই দেয়াল রচনা করে। সাকীর সুধায় মগ্নচৈতন্যের আভরণ হয়ে ওঠে না। প্রাণ খুলে বলতে পারি না “মদির আঁখির সুধায় সাকী ডুবাও আমার এ তনু মন”।
নজরুল নিজেই বিপদে ছিলেন তাঁর সবাক জীবনে। আমাদেরও বিপদে ফেলে গেছেন। কাণ্ডারি হুশিয়ার বললেও এখন কেউ আর হুশিয়ার হয় না। কারণ সে নিজে থেকেই বেশি বেশি হুঁশিয়ার হয়েই আছে। এতোটাই হয়েছে এখন, কবিকে সম্পূর্ণ ধরতেও পারছে না, সেই বোধটুকুও খুইয়েছে, আবার ছাড়তেও পারে না। ছাড়লে সে নিজেকেই খুঁজে পায় না। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীতসহ গোটা সত্তায় নজরুল নামটা তার প্রতিনিধিত্ব করেন, অন্তত রবীন্দ্রনাথ নামটির পাশে- এই ভেবে সে ঢোক গিলছে প্রতিদিন। সে আনন্দিত। ঠিক বিপরীতটাও আছে সমাজে। নজরুল যাদের জীবনে জড়িয়ে আছেন অতল প্রেমের আহ্বানে।
মুসলমান হয়ে শ্যামাসংগীত, কীর্তন, ভজন লিখে নিজেই গেয়েছেন। এরজন্য নন্দিত হয়েছেন, নিন্দিতও হয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল মঞ্চেই। রাণী রাসমনীর আদেশে তিনি গান গাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেয়েছিলেন সেদিন। শুধু একটি গানের কথাই যদি ধরি, “মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়...” এই গানটির বাণীর যে রূপক যে গভীরতা সেটা কি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি? যেখানে কবি বলছেন, “এই পূজা-বিলাস সংহার কর যদি পুত্র শক্তি নাহি পায়” - এটা বুঝি আমরা? পূজাকে কেন বিলাস বলেছেন কবি?
১৯৪১ সালে এইচএমভি থেকে গানটি প্রকাশিত হয়। সময়টা কেমন? ইতিহাস জানেনতো? গানটির প্রতিটি শব্দ নিয়ে কথা বলা যায়। অথচ আমরা না বুঝেই গেয়ে চলেছি। বিশেষ করে সনাতনীরা। তাই গান বিশ্বাস থেকে আসে না, সেখানে বিদঘুটে অন্ধকার। তাই সন্তানের দ্বিভুজে দশভুজার শক্তি আসে না। গান নিছক গানই থেকে যায়। বোধহীন, আত্মমর্যাদাহীন হুলুস্থুলে।
ইসলামী গান লিখেও নজরুল নিজ ধর্মীয় সমাজের মন জয় করতে পারেননি সবটুকু। সেখানেও নানা মত ও পথ। কাফের বলেছে তাঁকে নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরাই। তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দিয়ে ইসলামের তৌহিদের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন সেখানে প্রেমই ছিলো মুখ্য। খোদার প্রেম মানবপ্রেমের মধ্যেই নিহিত আছে এমন সহজ করে তাঁর আগে বাঙালিকে কেউ বলেননি। ইসলামী গানে তাঁর যে শব্দচয়ন ছিলো বাঙালির কাছে সে শব্দগুলো চিরচেনা হলেও তৌহিদের বাণীর উপস্থাপনে যেন নূতন করে ধরা দিয়েছিল।
"ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর..." এভাবে কেউ বলেছে তাঁর আগে?
আমরা কিন্তু সেখানেও প্রয়োজনের নজরুলকে খুঁজি, কাজে লাগাই। জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান হলেও এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে তাঁর পূর্বপুরুষের যে নাড়ীর টান, এ ভাবতীর্থের স্মৃতি-শ্রুতি-শাস্ত্র-সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাসের ধনঐশ্বর্যে তাঁরও যে রয়েছে উত্তরাধিকার সেটা তিনি ভুলে যাননি। ইসলাম সেখানে পথ আগলে দাঁড়ায়নি। উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুঁথি-পাঁচালী সবকিছু থেকেই তিনি ভাগ নিয়েছেন। সেই এক হাতেই তো বেজেছে অগ্নিবীণা আর বাঁশের বাঁশরী, একই কণ্ঠ থেকে এসেছে পার্থসারথির শাশ্বত বাণী, দ্রোহের বীজমন্ত্র। একই কলমে লেখা হয়েছে হামদ্ ও নাত আর পদাবলী কীর্তন। এমন মানুষ আর এমন বাঙালি আছে আর? নিজেকে জানতেই আজ তাঁকে বড্ড প্রয়োজন।
কবি নজরুল বাংলা গান ও কবিতার ভুবনে রবীন্দ্র যুগের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসা এক বিচিত্র ক্ষমতাবান কবি ও গীতিকার। খেয়াল, ঠুমরী, ধ্রুপদ, ধামার আর সেই নিধুবাবুর টপ্পার যুগে তিনিই বাঙালিকে সর্বপ্রথম আধুনিক প্রেমের গান শোনালেন। বাংলার পঞ্চকবি খ্যাত যারা ছিলেন তাঁরা নজরুল ইসলাম ছাড়া বাকি তিনজনই ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত বা তখনকার একটা নির্দিষ্ট ধাঁচের। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এঁদের গান অসামান্য অবদান রেখেছিল বাংলা গানের রবীন্দ্র প্রভাবের যুগে। তবে কবি নজরুল ছিলেন গুলবাগিচার বুলবুলি। অনন্য অসাধারণ। সাধক রামপ্রসাদ তখন তাঁর নিজস্ব একটি পরিচয় তৈরি করেছিলেন যদিও। অসাধারণ মাতৃপ্রেম ও ভক্তি রামপ্রসাদী গানে ফুটে উঠেছিল। নজরুল সেখানেও ভাগ বসাতে ভুল করেননি। তাঁর মাতৃসংগীতে সেটা লক্ষণীয়।
কবি হিসেবে তাঁর অবস্থান যেটুকু বাঙালির মনে তারচেয়ে ঢের বেশি একজন বহুমাত্রিক গীতিকার হিসেবে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাথে এক জায়গায় তাঁর মিল রয়েছে সেটা হচ্ছে নজরুলের গানই তাঁর প্রধান পরিচয়। নজরুলের গান আমাদের গাইতেই হবে। নেতাজী সুভাষ বসু তো বলই দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে, কারাগারে তাঁর গান গাওয়া হবে। যৌবনে প্রেম নিবেদনে নজরুল এখনো প্রাসঙ্গিক। হিন্দুর পূজা, মুসলমানের ঈদ নজরুলের গান ছাড়া চলে না এখনো। এটুকুই কি প্রয়োজন? সাম্যের কথা, মৈত্রীর কথা, কুলি-মজুরের কথা, শ্রমজীবী মানুষের কথা, বহ্নিশিখা নারীর কথা, জাতের নামে বজ্জাতির কথা, বিদ্রোহী কবিতার প্রতিটি শব্দব্রহ্মের কথা? আমরা মনে রাখবো? কোন নজরুল চাই আমাদের? মুসলমান নজরুল? মুসলিম জাগরণের নজরুল? মানুষ নজরুল? অখণ্ড নজরুল? নজরুলকে মনে হয় কেউ বুঝেনি। চোখ আর বুদ্ধির জোরে তা হয় না, অন্তরের ইশারায় যা পাওয়া যায়। উত্তম দ্রব্য উত্তম পাত্রেই রাখতে হয়। দুধ উত্তম হলেও পাত্র ভালো না হলে ছিঁড়ে যায়।
রবিহারা কবিতাটি পড়তে পড়তে নজরুলকে পেয়েছি। বিদ্রোহী কবিতার বিস্ময় নির্মাণে তাঁকে এখনো অবাক হয়ে খুঁজি। তাঁর গানে আমি ঐশী আনন্দে মগ্ন হই। তাঁর প্রবন্ধ আমার বিভাজিত সত্তায় শিহরণ জাগায়, জাগে আক্ষেপ।
নজরুলের গান নিয়ে, গানের বাণী, রূপক, উপমা, সুর এসব নিয়ে লিখতে গেলে শেষ হবে না সহসা। আবিলতা মুক্ত হতে পারলে লিখে যাবো এ আশা মনে আছে। আজ কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবনা লিখে গেলাম।
সাংবাদিক নজরুল যুগের দায় মিটিয়েছেন। নন্দন ভুবনে নয় যুদ্ধের ময়দানে রাইফেল কাঁধে নিয়েও গান গেয়েছেন, কবিতা লিখেছেন। কবিতা লিখে, পত্রিকা ছেপে কেউ জেলে গেছেন এবং জেলের ভেতরও গান ও কবিতায় দাবানলের বিধ্বংসী উত্তাপ ছড়িয়ে ব্রিটিশ রাজের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, অনশন করেছেন দীর্ঘদিন এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। দ্রোহের প্রতিজ্ঞায় স্বদেশ প্রেমে তিনি হয়েছিলেন উন্মাদ। নাগরিক মানুষ নন, নাগরিক হিসেব-নিকেশ, আপোষকামিতা ছিলো না তাঁর। এমন বিশাল হৃদয় নজরুলকে আমাদের ছোট মনে ধরা কঠিন। তাই সবখানেই প্রয়োজনটুকুই বিবেচ্য।
নজরুল কবে গুড়ের ব্যবসা করেছিলেন, কবে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কবে কোথায় ছাত্রী হোস্টেলে তাঁকে অপমান করা হয়েছিল, তিনি কেমন গরিব ছিলেন, লেটোর দলে চাকরি আর রুটির দোকানে কাজ, কার বাড়ি খেলেন, শেরেবাংলা তাঁকে কিভাবে টাকা না দিয়ে ঠকালেন, তাঁর চিকিৎসা নিয়ে কী কী হলো, রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁকে নিয়ে ঠেলাঠেলি এসবে আমার কোনো আগ্রহ নেই হে কবি। আমি তোমারই তোমারই তোমারই প্রেম চাই, অবিরাম বৃষ্টির মতো। এটুকুই আমার প্রয়োজনের নজরুল।
থাক গালাগালি, থাক সকল মূর্খতা, থাক বগল বাজানো সব আড়ম্বর। আমি খণ্ডিত, আমি বিভাজিত তবুও প্রয়োজনটুকু তুমি মিটিয়ে দাও।
আত্মভোলা মানুষ নজরুল। কতজন তাঁর কতকিছু নিয়ে গেছে। কতজন তাঁকে দিয়ে ফরমায়েশি গান লিখিয়েছে। তাঁর এসবে খেয়াল ছিলো না কখনো। ১৯৩৯ সালে দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম তিথি উপলক্ষে কোলকাতা বেতার আকাশবাণী থেকে 'শ্রী শ্রী চৈতন্যলীলাকীর্তন' নামক অনুষ্ঠানে তাঁর লেখা "বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়" গানটি প্রচারিত হয় যা পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এভাবেই কত সৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেছে কে জানে। সারাজীবন প্রতারিত হয়েছেন এ বেহিসাবি লোকটি। একের পর এক মৃত্যু তাঁকে চরম আঘাত করেছে। পুত্রশোকে পিতা কী অসাধারণ গান লিখেছেন,
“শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়, ফিরে আয় ফিরে আয়।
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়”
এই গানটি আমি অবাক বিস্ময়ে শুনি। কী অসাধারণ উপমা ও রূপক, কথার কী আবেগ, কী গভীরতা!
যে নজরুলের দু'ছত্র কবিতা বলতে পারে না, নজরুলের গান তার কণ্ঠে নেই, মনেও নেই, সে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের মাপটা দাঁড়িপাল্লায় ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। রবীন্দ্রনাথ তার কাছে শুধুই হিন্দু আর নজরুল তার প্রতিনিধি - সে এটাই ভাবে। সারাদেশে আজ নজরুলগীতি গাওয়ার শিল্পীর সংখ্যা কমে গেছে। অনেক শহরে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন। শিখছেও না সেরকম। কোথায় নজরুল চর্চা বলুন? নজরুলের প্রতি না আছে অকৃত্রিম প্রেম, না আছে আগ্রহ, না আছে ভক্তি-শ্রদ্ধা। আমাদের বিচিত্র সন্তুষ্টির জন্যই আছেন আমাদের দুখুমিয়া, নির্বাক ছবি হয়ে যাওয়া এককালের প্রচণ্ড নজরুল।
তবুও আশায় মানুষ বাঁচে। চলুক গবেষণা, চলুক পরিবেশনা, চলুক নানা নিস্ফলা আয়োজন, চলুক নীরস পাণ্ডিত্যের বকবকানি। যিনি মহাশ্মশানকেও নবনবীনের গান গেয়ে সজীব করে তোলার প্রতিজ্ঞা শোনান তিনি আমাদের ঘোর কাটাবেন। ততদিন
“আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আধখানা চাঁদ নিচে
প্রিয়া তব মুখে ঝলকিছে।”
এই দেখে দেখে অপেক্ষায় থাকি।
নিরঞ্জন দে: লেখক, প্রামাণ্যকার ও সংগঠক

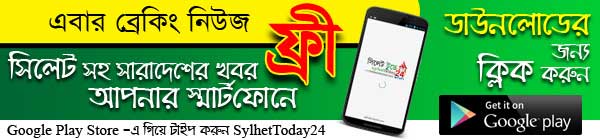
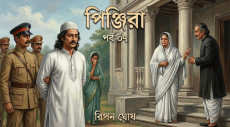
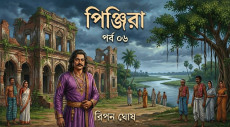
 IT Lab Solutions Ltd.
IT Lab Solutions Ltd.
আপনার মন্তব্য