
সাক্ষাৎকার : প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাকের অন্তর্দৃষ্টি
প্রকাশিত: ২০২৫-১১-০৯ ২১:০৯:১০

মিহিরকান্তি চৌধুরী:
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যবিদ, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বর্তমানে মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-এর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে দেশে ও বিদেশে চার দশকেরও বেশি সময়ের শিক্ষকতা ও গবেষণা-অভিজ্ঞতা তাঁকে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ সাহিত্য-মনস্ক শিক্ষাবিদে পরিণত করেছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। পি.এইচ.ডি.-তে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল “The Inherited Dichotomies: A Postcolonial Reading of the Major Novels of E. M. Forster, Mulk Raj Anand and Gabriel García Márquez”। প্রফেসর বসাকের একাডেমিক ও সৃজনশীল অবদান অত্যন্ত ব্যাপক—তিনি ৫৫টিরও বেশি প্রবন্ধ, বইয়ের অধ্যায় ও সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশ করেছেন এবং বিশ্বসাহিত্যের বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ত্রিশটি। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে E.M. Forster, Mulk Raj Anand and Gabriel García Márquez: A Postcolonial Reading of Inherited Dichotomies (জার্মানি, ২০১১) এবং Bangabandhu in Bengali Poetry (বাংলা একাডেমি, ২০২২), সাতশো বছরের ইংরেজি প্রেমের কবিতা (দ্বিভাষিক সংকলন, প্রকাশক: দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪) এবং দ্য প্রফেট (খলিল জিবরানের কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ)।
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০২০), ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড (২০২১) এবং শ্রুতি পুরস্কার (২০১০)-এর প্রাপক প্রফেসর বসাক একাধারে কবিতা, অনুবাদ ও সমালোচনার ক্ষেত্রেও স্বনামধন্য। তিনি পাবলো নেরুদা, খলিল জিবরান, এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর বহু রচনা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর গবেষণা, অনুবাদ ও সাহিত্যচিন্তা বাংলাদেশের ও বিশ্বসাহিত্যের পারস্পরিক সংলাপকে সমৃদ্ধ করেছে।
সম্প্রতি প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক তাঁর চার দশকের শিক্ষকতা, শিক্ষাদর্শন, গবেষণা ও সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতা এবং অনুবাদক ও লেখক হিসেবে জীবনের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে একটি গভীর, মননশীল সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, যা গ্রহণ করেছেন লেখক ও অনুবাদক মিহিরকান্তি চৌধুরী।
সংলাপকর্তা :
স্যার, ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আজকের আলোচনায় আমরা জানার চেষ্টা করব শিক্ষাজীবন, সাহিত্যদর্শন, অনুবাদচিন্তা এবং অধ্যাপক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতার নানা দিক। চার দশকেরও বেশি শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ নন, সাথে সাথে সাহিত্যচিন্তার ধারক, অনুবাদক ও মননশীল পাঠক। আপনার জীবনের যাত্রা, সাহিত্য ও অনুবাদের প্রতি নিবেদন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য শিক্ষাদর্শন। এই সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বে আমরা আলাপ শুরু করব আপনার শিক্ষাজীবন ও শিক্ষাদর্শন নিয়ে, যেখানে উঠে আসবে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষকতার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, ছাত্রজীবনের প্রভাব, ইংরেজি সাহিত্যের পাঠদান ও নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের জন্য প্রাসঙ্গিক পরামর্শ।
পর্ব ১ : শিক্ষাজীবন ও শিক্ষাদর্শন
সংলাপকর্তা : স্যার, আপনাকে অনেকেই জন্মগত শিক্ষক বলে মনে করেন। আপনার মতে আজকের দিনে একজন আদর্শ সাহিত্য-শিক্ষকের অপরিহার্য গুণাবলি কী কী?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : ধন্যবাদ। আমাকে জন্মগত শিক্ষক বলাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হলো। আমি খুশি হব যদি আমাকে কেবল একজন শিক্ষক বলা হয়, যার আবার লেখালেখির প্রতি কিছুটা বাড়তি ঝোঁক আছে যা সাধারণত সাবধানী মানুষ এড়িয়ে চলেন।
এবার সরাসরি প্রশ্নে আসি। ছাত্রজীবনে আমার অনেক প্রিয় সাহিত্য-শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আমার তরুণ ও সাহসী বিচার অনুযায়ী, তাঁদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। তাই পেশাজীবনে আমি সবার সেরা গুণগুলো বেছে নিয়ে একজন আদর্শ সাহিত্য-শিক্ষকের এক ধরনের সম্মিলিত প্রতিমূর্তি গড়ে নিয়েছিলাম। আমি সারা কর্মজীবন সেই প্রতিমূর্তিকে অনুকরণ করেছি, কিন্তু এর উচ্চতা কিংবা গভীরতায় কখনো পৌঁছাতে পারিনি।
একজন আদর্শ সাহিত্য-শিক্ষকের প্রথমত তাঁর বিষয়ের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সন্তোষজনক যোগাযোগ দক্ষতা থাকা জরুরি। এর বাইরে আমরা তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রেমের আন্তরিকতা, আজীবন শেখা ও শেখানোর মানসিকতা, এবং শিক্ষার্থীদের সামনে বৌদ্ধিক অন্বেষণের উপযোগী এক নতুন জগৎ উন্মোচনের দক্ষতা প্রত্যাশা করি। আর পুরো প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হলো পেশার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা ও অটল সততা।
সংলাপকর্তা : আপনি কখন শিক্ষাদানের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন? আপনার নিজস্ব ছাত্রজীবন কীভাবে আপনার শিক্ষকতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : সত্যি কথা বলতে কী, কখনোই মনে হয়নি আমি তাঁদের মতো হতে পারব—যাঁরা একদিন আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অন্তর্গত কোনো অজানা উপলব্ধি থেকেই বোধহয় ভেবেছিলাম, আমি হয়তো ভালো শিক্ষক হয়ে উঠব না। তাই সচেতনভাবেই শিক্ষকের পেশাকে আমার পছন্দের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু নিয়তির খেলাই অন্যরকম।
ছাত্রজীবনে আমি নানা ধরনের শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছি। কেউ কেউ ছিলেন প্রচুর পঠনপাঠনে মনোযোগী, চমৎকার বক্তা, সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তির অধিকারী—যাঁদের স্পর্শে ছাত্রজীবন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আবার কারো কাছে দেখেছি প্রস্তুতির অভাব, পাঠ্যবস্তুকে হালকা ছুঁয়ে যাওয়া, গভীরে না প্রবেশ করে কেবল ব্যাখ্যা-অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া। কেউ কেউ আবার ছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ, তবু গভীরতায় ভরপুর; তাঁদের আলোচনায় ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতো লেখকের প্রতিও, শিক্ষার্থীর প্রতিও।
এই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ছাত্র হিসেবে আমি শিক্ষকতার শক্তি ও দুর্বলতা উপলব্ধি করেছিলাম। পরবর্তীতে সেই উপলব্ধিই আমার শিক্ষাদানের ভঙ্গিকে গড়ে দিয়েছে—যেখানে দুর্বলতাগুলো বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর গ্রহণ করেছি সেই শক্তি, যা একজন সাহিত্যশিক্ষককে সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা দেয়।
সংলাপকর্তা : চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনি শিক্ষকতা করছেন। এই সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠদান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : এ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনের পরিক্রমায় দেখেছি—ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক্ষেত্র ধীরে ধীরে বহুগুণ প্রসারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে দেশের সর্বত্র ইংরেজি বিভাগগুলো মূলত ১৯২০–এর দশকের ব্রিটিশ সাহিত্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। অথচ একুশ শতকে এসে পাঠক্রম খুব বেশি হলেও ১৯৮০–এর দশকের বাইরে যায়নি।
এদিকে পোস্টমডার্ন ও পোস্টকলোনিয়াল সাহিত্য ধীরে ধীরে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক্রমে প্রবেশ করেছে। পোস্টকলোনিয়াল সাহিত্য যেহেতু উপনিবেশ-উত্তর জাতিগুলোর নিজস্ব সাহিত্য, তাই তা স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যবাহী ইংরেজি সাহিত্যের ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই পথেই প্রবেশ ঘটেছে ‘অন্য’ সাহিত্যের। একই সঙ্গে বিশ্বায়নের একাডেমিক তাগিদে আমেরিকান সাহিত্যও আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের পুনরায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে হয়েছে—যাতে নতুন ধারা ও নতুন লেখক নিয়ে কাজ করতে পারেন। যাঁরা এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, তাঁরা টিকে গেছেন; আর যাঁরা পারেননি, তাঁরা ক্রমে অচল হয়ে পড়েছেন।
এভাবে নানা সাহিত্যধারার ব্যাপক আগমনে প্রথাগত ইংরেজি সাহিত্য কিছুটা একলা হয়ে গেছে; এখন তাকে পড়তে হয় আমেরিকান, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকান, আফ্রিকান, এশীয় ও ক্যারিবীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এর ফল হলো—শিক্ষার্থীদের এমন বহু বিষয় মুখস্থ করতে হচ্ছে, যেগুলো ‘ইংরেজি সাহিত্য’ নামে আগে পরিচিত ছিল না।
কিন্তু এই বিপুল পরিসরকে যদি শিক্ষার্থীদের মানের ক্রমাবনতির সঙ্গে তুলনা করি, তবে বিষয়টি হয়ে ওঠে সত্যিই দুরূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মান অনেকটাই গড়পড়তা; মৌলিক ইংরেজি দুর্বল, পাঠ্যপুস্তক পড়ার আগ্রহ কম, ক্লাসে মনোযোগ নেই, গাম্ভীর্য ও আত্মপ্রেরণার অভাব স্পষ্ট। উপরন্তু, ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছেন সেই মহান শিক্ষকবৃন্দ, যাঁরা সাহিত্যপাঠে আলো জ্বালাতেন। সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠদান আজ আর আগের সেই দীপ্তি ধরে রাখতে পারছে না।
সংলাপকর্তা : আজকের ডিজিটাল প্রজন্মকে ক্লাসিক্যাল বা আধুনিক সাহিত্য পড়াতে গিয়ে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : প্রথমেই একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন—সাহিত্য, তা ক্লাসিক্যাল হোক, আধুনিক কিংবা উত্তর-আধুনিক, কোনোভাবেই ডিজিটাল প্রজন্মের সঙ্গে স্বভাবত বিরোধে যায় না। বরং ডিজিটাল প্রযুক্তি একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রকম প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের অ্যানালগ যুগে অসীম সম্পদে প্রবেশাধিকার কল্পনাতীত ছিল; আজকের শিক্ষার্থীরা মুহূর্তেই নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পৌঁছে যেতে পারে এবং সে পথে নিজেদের সমৃদ্ধও করতে পারে।
কিন্তু একই সঙ্গে, প্রস্তুতকৃত উত্তর—যেমন AI-নির্ভর বা গুগল-সন্ধানী উত্তরের ওপর নির্ভর করার প্রবণতা তাঁদের সৃজনশীল ও মৌলিক চিন্তাশক্তিকে বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তার ওপর সহজলভ্য উৎস থেকে নকল করার প্রবণতা শিক্ষার সততা ও বিশ্বস্ততাকে আঘাত করে। আসলে সাহিত্যপাঠ এক মানসিক যাত্রা; ডিজিটাল সরঞ্জাম এই যাত্রাকে সহজ করতে পারে, কিন্তু যদি ভুলভাবে ব্যবহৃত হয় তবে যাত্রাপথকেই কলুষিত করে।
সংলাপকর্তা : আপনার বিভাগে Outcome Based Curriculum (OBE) ও UGC–এর মানদণ্ড কীভাবে প্রয়োগ করেছেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : OBE মূলত দক্ষতাভিত্তিক বিষয়গুলোতে কার্যকর, যেখানে শিক্ষালাভের ফল সরাসরি ও স্পষ্টভাবে মাপা যায়। কিন্তু সাহিত্যের মতো বিষয়ে, যেখানে মূল জোর থাকে পাঠ্যের নানা ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনায়, সেখানে এর ফলাফল কেবল অনুভব করা যায়, স্পষ্টভাবে মাপা যায় না। OBE প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা ও ফলাফলের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে—যা সাহিত্যের সামগ্রিক ও মানবিক উপলব্ধিকে আড়াল করে ফেলে। শেকসপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথ হয়তো একজন শিক্ষার্থীকে আরও মহৎ ও প্রাজ্ঞ করে তুলতে পারেন, কিন্তু সেই প্রজ্ঞার দৈনন্দিন দক্ষতা কীভাবে মাপা যাবে—তার কোনো মানদণ্ড নেই।
UGC–এর মানদণ্ড তুলনামূলকভাবে অর্জনযোগ্য। তবে সর্বাঙ্গীণ অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি প্রায়শই পূর্ণরূপে মানদণ্ডে পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমাদের বিভাগে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি OBE ও UGC–এর লক্ষ্যমাত্রাকে এক টেকসই সমন্বয়ে আনতে—যতটুকু বর্তমান পরিস্থিতি অনুমতি দেয়।
সংলাপকর্তা : সদ্য শিক্ষকতায় প্রবেশ করা ইংরেজি সাহিত্যের নতুন শিক্ষকদের জন্য আপনি কী পরামর্শ দেবেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : প্রথমেই বলব—নিজেদের পুরোনো ভাষাগত ভুলগুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। এরপর পাঠ্যক্রমের সব লেখককে, এমনকি তার বাইরের লেখকদেরও গভীরভাবে পড়তে হবে। পাঠদানের আগে কোর্স পরিকল্পনা ও শ্রেণি-পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হতে হবে গভীর ও দ্ব্যর্থহীন, আর মূল্যায়নে থাকতে হবে পরম নিরপেক্ষতা। সবচেয়ে বড়ো কথা, কখনোই নিজের দক্ষতা নিয়ে আত্মতুষ্ট হওয়া চলবে না; তবেই আত্মোন্নয়নের জন্য জায়গা খোলা থাকবে।
শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে—তাঁরা শিক্ষক হয়ে উঠেছেন কারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী হিসেবে রয়েছে। তাই এই সম্পর্ককে সর্বদা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার । এই প্রথম পর্বে আমরা জানলাম আপনার চার দশকের শিক্ষকতা ও শিক্ষাদর্শন, আপনার সাহিত্যচিন্তা ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে সংযোগের দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষকের আদর্শ গুণাবলি, ছাত্রজীবনের প্রভাব, ইংরেজি সাহিত্যের পরিবর্তনশীল পাঠক্রম, ডিজিটাল প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ এবং নতুন শিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ—সবই একত্রে উঠে এসেছে আপনার সমৃদ্ধ শিক্ষাজীবন ও অনন্য শিক্ষাদর্শন।
শিক্ষকতার পাশাপাশি আপনি একজন সক্রিয় সাহিত্যচিন্তক। আপনার আলোচনায় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য কেবল পাঠের বিষয় নয়—এটি এক ধরনের জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনার অন্বেষণ এবং মানবিক অনুভূতির প্রতিফলন। এই পর্বে আমরা আপনার সাহিত্যচিন্তা, সৃজনধর্মী লেখা ও অনুবাদচিন্তার নানা দিক অনুসন্ধান করব।
পর্ব ২ : সাহিত্যচিন্তা ও সৃজনশীল লেখা
সংলাপকর্তা : আপনি ইংরেজি ও বাংলায় সমানভাবে দক্ষ লেখক। একটি নির্দিষ্ট ভাবনা কোন ভাষায় লিখবেন—তা কীভাবে ঠিক করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : ভাবনাটিই আমাকে বলে দেয় কোন ভাষায় তাকে রূপ দেওয়া প্রয়োজন। যদি তা আন্তর্জাতিক পাঠকের জন্য প্রযোজ্য হয়, ইংরেজি হয়ে ওঠে স্বাভাবিক মাধ্যম। আবার যদি ভাবনাটি কেবল বাংলাভাষী পাঠকের জন্য উপযোগী হয়, তবে বাংলাই হয়ে ওঠে সঠিক পছন্দ। আর তৃতীয়ত, যখন কোনো বাঙালি কবি বা লেখকের কীর্তি বিশ্বখ্যাত কবি-লেখকদের সমতুল্য হয়ে ওঠে, তখন আমি ইংরেজিতেই লিখি। যেমনটি করেছি শামসুর রাহমান বা মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে আমার কয়েকটি নিবন্ধে।
সংলাপকর্তা : অনেকে আপনাকে সৃজনশীল লেখকের চেয়ে অনুবাদক হিসেবে বেশি চেনে। আপনি কি মনে করেন আপনার মৌলিক লেখা প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : এটিকে আমি নিয়তির এক অদ্ভুত পরিহাস বলব। আমার সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসেবে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে আমি জাতীয় দৈনিকগুলোতে (সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, দ্য নিউ নেশন ইত্যাদি) নিয়মিত লিখতাম। অনেক নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্যসাংস্কৃতিক সংযোজনে। পরবর্তীকালে এই লেখাগুলো তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হয়— কালের কবিতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, সাহিত্য : নিকট সময় দূরের দেশ, এবং রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতা।
এরই মধ্যে সাহিত্যসম্পাদকরা নিয়মিত নতুন লেখা চাইতেন, যা সবসময় সম্ভব হতো না। তখনই শুরু হয় আমার অনুবাদযাত্রা। প্রবন্ধ ও অনুবাদের মধ্যে সময় ভাগ করে নিতে নিতে ধীরে ধীরে অনুবাদক হিসেবে আমার পরিচয় লেখকের পরিচয়কে ছাপিয়ে যায়। প্রকাশকরাও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন বলে আমার ধারণা; তাঁদের কাছে অনুবাদ যেন গদ্যরচনার তুলনায় বেশি বাজারযোগ্য মনে হয়েছে। আমার পুরোনো পাঠকেরা নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের সাক্ষী! তবে আমি এখনো মনে মনে আশা রাখি—যেদিন মনে হবে অনুবাদ সাহিত্যকে দেওয়ার মতো আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, সেদিন আমি আবার ফিরে যাব আমার প্রবন্ধকার-সত্তায়।
সংলাপকর্তা : আপনার ডক্টরাল গবেষণায় তিনজন প্রতীকী লেখককে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পোস্টকলোনিয়াল কাঠামোয় কীভাবে ই. এম. ফর্স্টার, মুলক রাজ আনন্দ ও গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আমার ডক্টরাল গবেষণা ছিল এক তুলনামূলক সমালোচনামূলক অনুসন্ধান—যেখানে তিন মহাদেশের তিন মহৎ লেখককে (ইউরোপের ই. এম. ফর্স্টার, এশিয়ার মুলক রাজ আনন্দ এবং লাতিন আমেরিকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস) একই বিশ্লেষণচক্রে আনা হয়েছিল। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করেছেন—ঔপনিবেশিক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক, আর উত্তর-ঔপনিবেশিক থেকে নবঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত। তাঁদের রচনাকে আমি পোস্টকলোনিয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছি, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দ্বন্দ্ব ও জটিলতা।
ই. এম. ফর্স্টার ছিলেন এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক, যাঁর মনোযোগ ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের দিকে এবং তার কল্পিত উত্তর-ঔপনিবেশিকতার আকাঙ্ক্ষায়। মুলক রাজ আনন্দ লিখেছেন ভারতীয় উপনিবেশিক ব্যাধি ও স্বাধীনতা-উত্তর আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত প্রেক্ষাপটে। আর গার্সিয়া মার্কেস, যিনি কলম্বিয়ার স্বাধীনতার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ করেছেন কিভাবে তাঁর মহাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল—দেশীয় একনায়কের উত্থান ও বিদেশি নবঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশে।
এই তিনজন লেখককে পোস্টকলোনিয়াল সংকটে প্রাসঙ্গিক করে তোলে তাঁদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি—যেখানে ঔপনিবেশিকতা কখনোই পুরোপুরি বিদায় নেয় না; বরং নতুন নামে, নতুন আড়ালে ফিরে আসে, কিন্তু ধরে রাখে সেই প্রাচীন ঔপনিবেশিক আত্মা। যেমন জাঁ-পল সার্ত্র যথার্থই বলেছেন—এ এক অন্তহীন "নরকীয় চক্র"।
সংলাপকর্তা : আপনার সৃজনধর্মী বইগুলোর মধ্যে কোনটিকে আপনি নিজে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, এবং কেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : এ প্রশ্ন যেন এক অভিভাবককে জিজ্ঞেস করার সমান—তাঁর প্রিয় সন্তান কে? উত্তর দেওয়াটা সহজ নয়। আমি সে বিচার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিই; তাঁরাই স্থির করবেন কোনটি উৎকৃষ্ট, আর কোনটি কম গ্রহণযোগ্য। তবে এটুকু যোগ করব—আমার তথাকথিত সৃজনধর্মী বইগুলো আসলে নিছক সৃজনশীলতার প্রকাশ নয়; এগুলো অনেকাংশেই সমালোচনামূলক অনুসন্ধান।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার, আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। আপনার বক্তব্যে চম]কারভাবে উঠে আসল কীভাবে ভাষা, সাহিত্যধারা, গবেষণা ও অনুবাদ একত্রে আপনার সাহিত্যদর্শনের আকাশকে সমৃদ্ধ করেছে এবং নতুন প্রজন্মের পাঠক ও লেখকদের জন্য শিক্ষণীয় ধারণা প্রদান করেছে।
স্যার, এই পর্বে আমরা আপনার গবেষণা ও প্রজ্ঞার দিকে মনোযোগ দেব। চার দশকেরও বেশি শিক্ষকতা ও সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতার পর, আপনি যেভাবে পিএইচডি করেছেন, সৃজনধর্মী লেখা করেছেন এবং বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন—সেগুলো আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণার গল্প। এই পর্বে আমরা জানতে চাই—আপনার গবেষণার যাত্রা, প্রজ্ঞার উৎস, এবং একজন গবেষক হিসেবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে।
পর্ব ৩ : গবেষণা ও প্রজ্ঞা
সংলাপকর্তা : জীবনের তুলনামূলক পরিণত বয়সে আপনি পিএইচডি করেছেন। আপনাকে কী প্রেরণা দিয়েছিল আনুষ্ঠানিক গবেষণায় ফেরত যেতে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : প্রাজ্ঞজনেরা বলেন—““দেরিতে হলেও ভালো।” তাই আমিও আমার প্রৌঢ় বয়সে পিএইচডি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সত্য বলতে কী, পিএইচডি ডিগ্রি কোনো জ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষা নয়; বরং একধরনের অনুমতিপত্র—অ্যাকাডেমিয়ার তথাকথিত অভিজাত পরিসরে প্রবেশের যোগ্যতার প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ছাড়া শিক্ষকতা করা তখনও, এখনও, খুব মর্যাদাপূর্ণ নয়। সম্ভবত সেটিই ছিল আমার সবচেয়ে যথার্থ কারণ।
সংলাপকর্তা : আপনার ডক্টরাল গবেষণাপত্র রচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলবেন? বিশেষত, এর চ্যালেঞ্জ ও অর্জনের দিকগুলো?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : চ্যালেঞ্জের অভাব ছিল না। প্রথমেই বলি—আমি ছিলাম নিখাদ অ্যানালগ মানুষ, যে একটি সাধারণ কম্পিউটার চালাতেও অক্ষম, টাইপিং বা ব্রাউজিংয়ের ন্যূনতম জ্ঞানও ছিল না। তাই গোটা গবেষণাপত্র আমাকে হাতে লিখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারে যাওয়ার সুযোগ ছিল অতি সীমিত। ফলে প্রয়োজনীয় সব টেক্সট ও রেফারেন্স বই দেশ-বিদেশ থেকে কিনতে হয়েছে। আমার কিছু বন্ধু যুক্তরাজ্য থেকে সিলেট পর্যন্ত বিশাল বোঝা বই টেনে এনেছেন; আমার প্রথম সুপারভাইজার এমনকি লন্ডনের লাইব্রেরি থেকে দুর্লভ কাগজপত্র ফটোকপি করে পরে পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, চারপাশে কোনো সহকর্মী ছিল না যার সঙ্গে মেধার আদান-প্রদান করতে পারি। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় সুপারভাইজার আমার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার ওপর এত আস্থা রেখেছিলেন যে, পুরো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ভার আমাকে একাই বহন করতে হয়েছিল।
অর্জনের দিকে আলোকপাত করি। প্রথম অর্জন তো ডিগ্রিটিই। দ্বিতীয়ত, সেমিনারে যখন অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে আমি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি, তাদের সামান্য খোঁচা-টিপ্পনিগুলোও শোভনভাবে গড়িয়ে গেছে—সে অভিজ্ঞতা ছিল স্মরণীয়। আর চূড়ান্ত অর্জন এটাই যে, বহিঃপরীক্ষকরা ও আমার সুপারভাইজার একসঙ্গে আমার গবেষণাপত্রকে বিন্দুমাত্র সংশোধন ছাড়াই, নির্ভুল হিসেবে অনুমোদন দিয়েছিলেন। টানা তিন বছরের ক্লান্তিকর পরিশ্রম শেষে সেটিই ছিল প্রকৃত মুক্তির মুহূর্ত।
সংলাপকর্তা : আপনার গবেষণায় পোস্টমডার্ন ও পোস্টকলোনিয়াল উভয় তত্ত্বই স্থান পেয়েছে। এসব সমালোচনামূলক কাঠামো কীভাবে আমাদের সমকালীন সাহিত্যবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : যেমন সাহিত্যের জগৎ নিজেই ক্রমাগত বিভাজনমুক্তি ও সংশোধনের ভেতর দিয়ে গেছে, তেমনি সাহিত্যতত্ত্বও গেছে কঠোর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। একটি পোস্টকলোনিয়াল পাঠ সমানভাবে পোস্টমডার্ন হতে পারে; আবার কেবলমাত্র উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে রচিত হলেই তা চেতনার বাহক হয়ে পোস্টকলোনিয়াল হয়ে ওঠে না। তাই সমালোচনামূলক কাঠামো কোনো শেকল নয়; বরং কিছু কার্যকরী হাতিয়ার। মূলপাঠই এগুলোকে পথ দেখায়—তত্ত্ব নয়।
সংলাপকর্তা : আপনার গবেষণা ও সৃজনশীল সাধনা—দুটির মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : সাধারণত দুটো একসঙ্গে চলে না। একটির জন্য জায়গা করে দিতে হয় অন্যটিকে। উভয়েরই প্রয়োজন ব্যাপক পাঠ, গভীর চিন্তা ও দীর্ঘ পরিকল্পনা। দীর্ঘ গবেষণা শেষ করলে আমি সম্পূর্ণভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ি। তখন আসে এক নিস্তব্ধ বিরতির সময়। সেই বিরতির পরই সৃজনশীল লেখার জন্য উপযুক্ত মুহূর্ত তৈরি হয়। এভাবেই একটির পর আরেকটি ক্রমশ এগিয়ে চলে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাদানের দায়িত্বের সমান্তরালে। গবেষণা পূরণ করে দেহের ক্ষুধা, আর সৃজনশীলতা প্রশমিত করে মনের ক্ষুধা।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার, এই আলোচনায় উঠে আসল আপনার গবেষণার উদ্দেশ্য, সমকালীন সাহিত্য-বিশ্বকে অন্বেষণ করার পদ্ধতি, সৃজনশীলতা ও জ্ঞানচর্চার ভারসাম্য, এবং অনুবাদের নৈতিক ও শিল্পগত দিক। আমরা জানতে পারলাম কীভাবে প্রজ্ঞা, অধ্যবসায় ও মানবিক অন্তর্দৃষ্টি একত্র হয়ে আপনার সাহিত্য ও শিক্ষাজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।
আপনি বাংলাদেশের অন্যতম সফল অনুবাদক। খলিল জিবরান, পাবলো নেরুদা, গার্সিয়া মার্কেস—বিশ্বসাহিত্যের নানা মহীরুহকে আপনি বাংলায় নিয়ে এসেছেন। অনুবাদ আপনার কাছে কতটা শিল্প, আর কতটা দায়িত্ব—এই প্রশ্ন থেকেই শুরু করি।
পর্ব ৪ : সাহিত্যশিল্প হিসেবে অনুবাদ
সংলাপকর্তা : অনুবাদকে প্রায়ই সংস্কৃতির সেতু বলা হয়। আপনি সাহিত্য-অনুবাদকে কীভাবে দেখেন—একজন ব্যাখ্যাকারক হিসেবে, নাকি সৃজনশীল সহলেখক হিসেবে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : অনুবাদ সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায় তবে তা সীমিত মাত্রায়। এখানে রয়েছে বিদেশীকরণের ঝুঁকি, আবার আছে দেশীয়ীকরণেরও বিপদ। অনুবাদককে তাই ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপটের দুই প্রান্তের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো অনুবাদককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বিশেষ পরিভাষা ব্যাখ্যা করতে হয়, যাতে লক্ষ্যভাষার পাঠকের জন্য পাঠ্যটি বোধগম্য হয়। সহলেখকত্বের প্রসঙ্গে বলতে হয়, অনুবাদক কোনোভাবেই সেই দাবিদার নন—এ ধারণা নিজেই হাস্যকর। অনুবাদক সর্বোচ্চ যা হতে পারেন, তা হলো এক নীরব সহযাত্রী, মূল লেখকের কপিরাইটের দখলদার নন। শেষ পর্যন্ত, মূল পাঠ্যের সাথে ছলচাতুরী করা প্রতারণার সামিল। অনুবাদক কখনোই মূল লেখকের ঊর্ধ্বে যেতে পারেন না; অনুবাদককে সর্বদা মূল লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয়।
সংলাপকর্তা : কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে আপনি সবচেয়ে বড়ো কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, বিশেষত সংস্কৃতিমণ্ডিত বা প্রবচননির্ভর কবিতায়?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : কবিতা অনুবাদ করতে হলে অনুবাদকের ভেতরও একজন কবির উপস্থিতি চাই। কবিতার ভাষা কেবল ভাষাগত নয়—তার নিজস্ব এক ব্যঞ্জনাময় রীতি আছে, যা রূপক ও বহুস্তরীয় অর্থে ভরা। এ এক ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ। যেমনটি হয়েছিল খলিল জিবরানের The Prophet অনুবাদ করতে গিয়ে। আবার কিছু কবিতার সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন অ্যালেন গিন্সবার্গের Howl ও Kaddish–এ প্রকাশ্য যৌনতার বিবরণ আমাদের রক্ষণশীল সমাজে অশ্লীল বলে বিবেচিত। সেক্ষেত্রে আমাকে আক্ষরিক অনুবাদ এড়িয়ে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য ‘রূপসজ্জিত’ অনুবাদের পথে হাঁটতে হয়েছে। উদার সাহিত্যের রচনা যখন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ভাষায় রূপান্তরিত হয়, তখন অনুবাদকের জন্য তা এক কঠিন পরীক্ষার সময়।
সংলাপকর্তা : কোন বিশ্বসাহিত্য বা বাংলা ক্লাসিক অনুবাদ করবেন তা আপনি কীভাবে ঠিক করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : কিছু নীরব নিয়ম মানি আমি। প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করি—আমি কি পাঠ্যাংশটি ভালোবাসি? যদি ভালোবাসি, তবে এগোই; যদি না লাগে, কোনো প্ররোচনাই আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কাজটি আমার মানসিক সুরের সঙ্গে মানানসই কি না। সব লেখা—বাংলা হোক বা ইংরেজি—আমার মানসিক তরঙ্গে ধ্বনিত হয় না। তাই আমি বেছে নিই সেগুলোই, যেগুলো আমার সংবেদনশীলতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। শেষত, অনুবাদযোগ্যতার বিষয়টি আগে যাচাই করি। মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া অনুবাদের কোনো মানে হয় না।
সংলাপকর্তা : জটিল কোনো পাঠ, যেমন খলিল জিবরানের The Prophet, বাংলায় অনুবাদ করার প্রক্রিয়া কেমন ছিল?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : প্রথম পাঠেই The Prophet আমাকে মুগ্ধ করেছিল—তার রহস্যময় আকর্ষণ উপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু এই আকর্ষণই অনুবাদের যথেষ্ট কারণ ছিল না। আমাকে বিস্মিত করেছিল—এই গ্রন্থের বহু প্রসিদ্ধ অনুবাদেও ভয়াবহ ভুল দেখতে পাওয়া। তখনই আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, এমনকি দ্বিভাষিক বিন্যাসে উপস্থাপনের সাহস করেছিলাম, যাতে পাঠক মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি রেখে নিরন্তর তুলনা করতে পারেন। আমি একটি বিশদ ভূমিকাও সংযোজন করেছিলাম, যেখানে ব্যাখ্যা করেছি কেন পূর্বে চার-পাঁচটি অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আরেকটি অনুবাদ প্রয়োজনীয় হলো।
পূর্ববর্তী অনুবাদগুলির দুর্বলতা আমি চিহ্নিত করেছিলাম, যা আমাকে তীব্র সমালোচনার মুখে ফেলতে পারত। সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু হয়নি; বরং বইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, বহুবার মুদ্রিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর পেয়েছে।
সংলাপকর্তা : অনুবাদে আবেগগত বিশ্বস্ততা ও নান্দনিক আবেদন কীভাবে বজায় রাখেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আবেগগত বিশ্বস্ততা অনুবাদের মৌলিক শর্ত—বিশেষত প্রেমের কবিতা অনুবাদে। এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম ৭০০ বছরের ইংরেজি প্রেমের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে। আবার টি. এস. এলিয়ট অনুবাদে আমাকে চরম আত্মবিলোপের চর্চা করতে হয়েছিল।
নান্দনিক আবেদন মূলত ধরে রাখার বিষয়, সৃষ্টি করার নয়। মূল টেক্সটে যদি আবেদন থাকে না, অনুবাদক তা জোর করে জুড়ে দিতে পারেন না; আর যদি জুড়েও দেন, তবে তা তাঁর অনুবাদকুশলতার মায়াজালে, কিন্তু মূল লেখায় হস্তক্ষেপ করে নয়। সৌন্দর্যের ভিত্তি থাকে মূল লেখকের হাতে, আর অনুবাদের সাফল্য নির্ভর করে অনুবাদকের দক্ষতায়। মনে পড়ুক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সেই মন্তব্য—গ্রেগরি রাবাসা তাঁর One Hundred Years of Solitude–এর ইংরেজি অনুবাদ এতই অনবদ্য করেছিলেন যে লেখক নিজেই বলেছিলেন: “ইংরেজি অনুবাদ আসল স্প্যানিশ গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”
সংলাপকর্তা : আপনি বিভিন্ন মহাদেশের সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। লাতিন আমেরিকা থেকে এশিয়া—ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা কীভাবে সামলান?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আমি সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছি বিপুল পরিমাণ কবিতা সংকলন—যেমন বিশ শতকের বিশ্বকবিতা, বিশ শতকের লাতিন আমেরিকার কবিতা, এশিয়ার কবিতা, বিশ্বকবিতায় নারীস্বরে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কবিতা ইত্যাদি। মহাদেশ বা শতক নির্দিষ্ট কোনো সংকলনের কাজ হাতে নেওয়ার আগে আমাকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করতে হয়েছে।
এ ধরনের কাজে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর যেমন কঠিন, তেমনি বিদেশি নাম বাংলায় লিপ্যন্তর করাও জটিল। এজন্য ফোনেটিক গাইড ও উচ্চারণ-সংক্রান্ত ভিডিও কাজে লেগেছে। তবুও উচ্চারণের অরাজকতা রয়ে গেছে—একটি স্প্যানিশ নামের একাধিক বৈধ উচ্চারণ পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এমন অনুবাদ প্রকল্প শুরু করার আগে অনুবাদককে করতে হয় নিদারুণ পরিশ্রম; তারপরই আসল অনুবাদের কাঠামো গড়তে শুরু করে।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার, আমরা আসলেই সৌভাগ্যবান যে খলিল জিবরান, পাবলো নেরুদা, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসসহ বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন মহীরুহকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রক্রিয়া, চ্যালেঞ্জ, নৈতিক ও নান্দনিক বিষয়গুলো অঅপনি আলোচনা করলেন। এছাড়া, কবিতা ও প্রবন্ধ অনুবাদে আবেগগত বিশ্বস্ততা, সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা, ভাষাগত ভারসাম্য ও পাঠকের সঙ্গে সংবেদনশীল সংযোগ রক্ষা—সবই উঠে এসেছে । আমরা আরো জানতে পারলাম, কীভাবে একজন অনুবাদক মূল লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহলেখকত্বের সংবেদন ও শিল্পীচর্চাকে ধারণ করেন, এবং এই কাজের সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রভাব তিনি কীভাবে উপলব্ধি করেন।
আপনার সাহিত্যজীবন যেমন বহুমাত্রিক, তেমনি সমৃদ্ধ পুরস্কার ও স্বীকৃতিতেও। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড, শ্রুতি পুরস্কার—সবই আপনার সাহিত্য ও অনুবাদে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি। কিন্তু এই সম্মানগুলো শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক অভিঘাতও সৃষ্টি করে। এই পর্বে জানতে চাই—আপনি সাহিত্যসম্মানকে কীভাবে দেখেন, এবং সমাজে এর প্রভাবকে কীভাবে উপলব্ধি করেন?
পর্ব ৫ : সাহিত্যসম্মান ও সামাজিক অভিঘাত
সংলাপকর্তা : ২০২০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কী অর্থ বহন করে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : এ নিয়ে সন্দেহ নেই যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার একটি আকাঙ্ক্ষিত সম্মাননা—এ এক ধরনের জাতীয় স্বীকৃতি। তবে আমি কখনো কোনো পুরস্কারের পেছনে ছুটিনি, কখনো লবিংও করিনি। আমার সময় কেটেছে সৃষ্টিশীলতা ও অনুবাদের কাজে, কোনো পুরস্কারের লোভ ছাড়াই। তাই এক সন্ধ্যায় যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোন এলো এবং মহাপরিচালক আমাকে অভিনন্দন জানালেন, আমি ভদ্রভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। সংবাদটি অবশ্যই আনন্দের ছিল তবে সংযমী মানুষ হিসেবে আমি আনন্দে নাচতে কিংবা শোকে ভেঙে পড়তে শিখিনি। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, এই প্রাপ্তি আমার আপনজনদের আনন্দ দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পেশাগত দিক থেকে তেমন কোনো আলোড়ন তোলেনি—কারণ, শেষ পর্যন্ত এমন পুরস্কারপ্রাপ্তরা আমাদের আশেপাশে খুব কম তো নয়!
সংলাপকর্তা : আপনার মতে, বাংলাদেশের সাহিত্য পুরস্কারগুলো কি অনুবাদকদের সাহিত্য সংস্কৃতি গঠনে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আমি নিশ্চিত নই। অনুবাদকদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভূমিকা তুলে ধরতে পুরস্কারের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। পুরস্কার-পরবর্তী সময়ে অনুবাদকরা যা করেন, তা তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগেই করেন, বাইরের কোনো উৎসাহ বা প্রণোদনায় নয়। দুঃখজনকভাবে পুরো বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায়, কোনো সমন্বিত অনুসরণ বা ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না।
সংলাপকর্তা : দ্বিভাষিক ও অনুবাদভিত্তিক গবেষণাকে উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : বাংলা একাডেমির মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—কেবল বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বাছাই করা অনুবাদ প্রকাশেই তারা সীমাবদ্ধ থেকেছে। কোনো সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা আমরা দেখতে পাইনি। ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বহু আগে থেকেই অনুবাদ বিভাগ চালু করেছে—যেখানে সার্টিফিকেট কোর্স থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত সুযোগ আছে। বিপরীতে, বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো অনুবাদ বিভাগ নামে কোনো পূর্ণাঙ্গ বিভাগ স্বপ্নমাত্র। সর্বোচ্চ যা হয়েছে তা হলো—সাহিত্য বিভাগে একটি কোর্স চালু করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।
সংলাপকর্তা : আপনার অনুবাদগুলো শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক ও সাহিত্য সমাজে কী প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আমরা যেন না ভুলি—গ্রিক, রোমান, পারস্য বা প্রাচীন ভারতের যে বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার আমাদের কাছে এসেছে, তা মূলত অনুবাদের মাধ্যমেই। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, রুমি, খৈয়াম—তাঁদের আমরা অনুবাদের জানালায়ই চিনি। আজও স্প্যানিশ, জাপানি, চীনা বা আরবি ভাষায় কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রকাশিত হলে কয়েক মাসের মধ্যে তা অনুবাদ হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছে যায়। কারণ অনুবাদ ঢুকে পড়েছে শ্রেণিকক্ষে, গৃহ-গ্রন্থাগারে, স্থানীয় বইয়ের দোকানে ও সাহিত্য সভায়। এ থেকেই বোঝা যায়—অনুবাদের বিপুল জনপ্রিয়তা।
আমার নিজের অনুবাদের প্রভাব নিয়ে বলতে গেলে, ইংরেজি বিভাগের বহু শিক্ষার্থী এগুলোকে পাঠ্যতালিকায় পড়েছে বলে শুনেছি। সাধারণ পাঠকের কাছে এর আবেদন মাপা যায় পুনর্মুদ্রণ ও একাধিক সংস্করণের সংখ্যা দিয়ে। সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেও এ অনুবাদগুলোকে ঘিরে এক নির্দিষ্ট আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার, এই পর্বে আমরা জানলাম ও শিখলাম, সাহিত্যসম্মান ব্যক্তিগত স্বীকৃতি হলেও সমাজে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে এবং অনুবাদ শিক্ষার্থী, পাঠক ও সাহিত্যসমাজকে সমৃদ্ধ করে। প্রফেসর বসাকের উদাহরণ দেখায়, সৃষ্টিশীলতা ও অনুবাদকর্মের মাধ্যমে একজন সাহিত্যিক সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।
শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে আপনার অবদান যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি আপনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্বেও ছিলেন নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে। নেতৃত্ব শুধু পদ নয়, এটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও বটে। এই পর্বে জানতে চাই—প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, এবং আপনি নেতৃত্বকে কীভাবে একটি বৌদ্ধিক দায় হিসেবে দেখেন?
পর্ব ৬ : প্রতিষ্ঠানগত নেতৃত্ব ও জনমনীষী ভূমিকা
সংলাপকর্তা : মেট্রোপলিটান বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স স্কুলের ডিন এবং ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে আপনি প্রশাসনিক দায়িত্ব ও একাডেমিক ও সাহিত্যিক জীবনের ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে—যিনি রান্না করেন, তিনিই চুলও বেঁধে নেন। আমি দৈনিক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে কাজ করি, যাতে একটির প্রয়াস অন্যটির পথে বাধা না সৃষ্টি করে। প্রয়োজন হলে, আমি সাহিত্যিক দায়িত্বকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখি, যাতে আমার নিয়োগকৃত কাজের ন্যায়সঙ্গত পূর্ণতা দেওয়া যায়।
সংলাপকর্তা : আজকের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্য শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও নৈতিক দিশা গঠনে কী ভূমিকা রাখে?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : সাহিত্য আমাদের মানুষের সম্পর্কের জটিলতা বোঝাতে সাহায্য করে এবং মূল্যবোধ, সততা ও সহানুভূতির পাঠ দেয়—যা বাণিজ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায়শই দিতে ব্যর্থ হয়। সাহিত্য শিক্ষার্থীর জীবনদৃষ্টিকে বিস্তৃত করে, বোঝাপড়াকে গভীর করে এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত করে। শিক্ষার্থীদের কাছে সাহিত্য এক আয়না, যেখানে তারা বাস্তব ও কাল্পনিক দু’দিক থেকেই নিজেদের জীবন দেখতে পায়।
সংলাপকর্তা : উচ্চশিক্ষায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা একজন হিসেবে, আপনি বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও হিউম্যানিটিজ পড়ানোর ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন দেখতে চাইবেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : উচ্চশিক্ষায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাহিত্য ও মানবিকবিদ্যার পাঠদানে পশ্চিমা ও প্রাচ্য ধারা—দুইয়ের একটি সৃজনশীল সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। অর্থাৎ, “নিজভূমি” ও “বিশ্ব”–এর মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে।
দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য প্রায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ স্যার, এই পর্বে আমরা দেখলাম, আপনি প্রশাসনিক ও একাডেমিক দায়িত্বকে কীভাবে সুসমন্বিত রাখেন এবং উচ্চশিক্ষায় সাহিত্য ও মানবিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা কী। অঅপনার কাছ থেকে দৃঢ়ভাবে জানা হলো, সাহিত্য শুধু পাঠ্যবিষয় নয়—এটি শিক্ষার্থীকে নৈতিক দিকনির্দেশনা, মানবিক বোধ ও জীবনের গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য মূল শিক্ষা হলো, জ্ঞানার্জন ও সৃজনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রাখা, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, এবং সততা ও উদারতার সঙ্গে জীবন ও পেশাগত দায়িত্ব পালন করা। এই পর্ব আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠানগত নেতৃত্ব ও বৌদ্ধিক দায়িত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ কেমন হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।
প্রত্যেক প্রজন্মই পূর্বসূরিদের কাছ থেকে আলো নেয়, পথ খুঁজে নেয় তাদের জীবন ও চিন্তার ভেতর দিয়ে। আপনি বহু প্রজন্মের শিক্ষক, পরামর্শদাতা ও প্রেরণার উৎস। স্যার, জানতে চাই—বর্তমান প্রজন্মকে আপনি কী বলতে চান? তাদের জন্য আপনার জীবন থেকে নেওয়া মূল শিক্ষা কী হতে পারে?
পর্ব ৭ : পরামর্শ ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বার্তা
সংলাপকর্তা : বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ বাংলাভাষী বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী তরুণ অনুবাদকদের আপনি কী বার্তা দিতে চাইবেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আমি চাইব—যেখানে স্বর্গদূতও ভয় পায়, সেখানে হঠাৎ না ঝাঁপিয়ে ধৈর্য ধরুন। আমার বিনম্র পরামর্শ—পাঠ্যটি পড়ুন, পুনঃপড়ুন, আরও একবার পড়ুন, গভীর অর্থে পৌঁছান, ভাষা ও গঠন বিশ্লেষণ করুন, খসড়া তৈরি করুন এবং পুনঃখসড়া করুন, তারপরই চূড়ান্ত রূপের দিকে যান। প্রকাশনার তাড়াহুড়া করবেন না, সময় দিন এবং নিজের কাজকে নিজেই সম্পাদনা করুন। যখন আপনি বিশ্বাস করবেন—আপনার অনুবাদ মূলের সমতুল্য, তখনই প্রকাশকের দরজায় কড়া নাড়ুন।
সংলাপকর্তা : বিভ্রান্তিময় এই যুগে, তরুণ কবি ও লেখকদের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়ার মূল কী বলে আপনি মনে করেন?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : এটি হয়তো অনিচ্ছাকৃত পরামর্শ মনে হতে পারে। আমার মতে, জ্ঞান যখন বিভাজনমুক্ত হয়েছে, তখন উদীয়মান কবি বা লেখককে সর্বদা আপডেট থাকতে হবে। জানা গুরুত্বপূর্ণ—অতীত ও সমসাময়িক লেখকেরা কী লিখছে, যেন আপনি কন্টেন্ট ও শৈলীতে তাঁদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারেন। নাহলে এটি হবে ২১শ শতকে ১৯শ শতকের অনুকরণমূলক চেষ্টা করা।
সংলাপকর্তা : তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য যদি একমাত্র চিরকালীন শিক্ষণীয় বাণী দিতে হতো, তা কী হতো?
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : নিজের কথায় বলতে গেলে, আমার দারুণ অভাব জ্ঞানের। চিরকালীন প্রজ্ঞা আসে সক্রেটিসদের মতো মহাজ্ঞানের কাছ থেকে। তাই, আমাকে ক্ষমা করুন—আমি সেই যোগ্য নই।
সংলাপকর্তা : ধন্যবাদ, স্যার। এই শেষ পর্বে আমরা তরুণ অনুবাদক, লেখক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শ শুনলাম। আপনি ধৈর্য, পুনঃপাঠ, বিশ্লেষণ ও আত্ম-সম্পাদনার গুরুত্বকে তুলে ধরলেন অনুবাদের ক্ষেত্রে। তরুণ লেখকদের জন্য আপনার বার্তা হলো—নিজের স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠস্বর খুঁজে বের করতে ইতিহাস ও সমসাময়িক সাহিত্যকে জানার সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনার অন্বেষণ অপরিহার্য। পাশাপাশি, আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি বিনম্র থাকা ও শিক্ষার ধারাকে চিরজীবনের অংশ করা প্রয়োজন। এই পর্ব আমাদের জন্য তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেওয়া, সাহিত্যিক ও শিক্ষণীয় জীবনের মূল্য বোঝার একটি সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী দিকনির্দেশ হয়ে উঠেছে।
স্যার, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আপনার শিক্ষকতা জীবন, গবেষণা, লেখক জীবনসহ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য। আপনাকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই।
প্রফেসর ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক : আপনাকেও শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

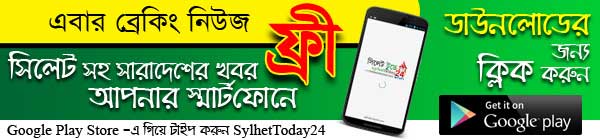


 IT Lab Solutions Ltd.
IT Lab Solutions Ltd.
আপনার মন্তব্য